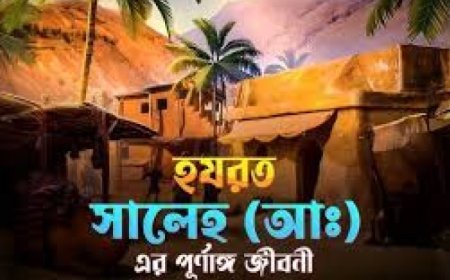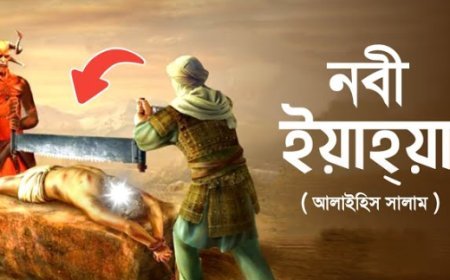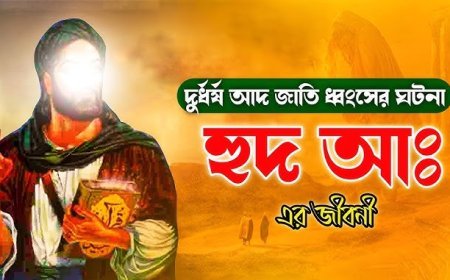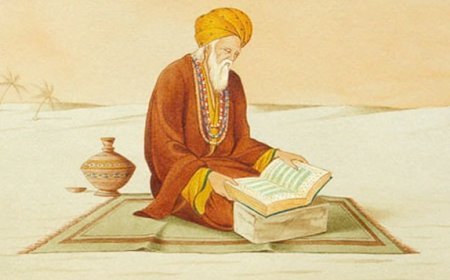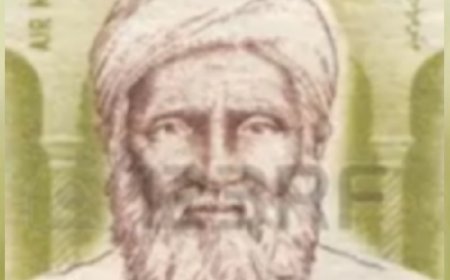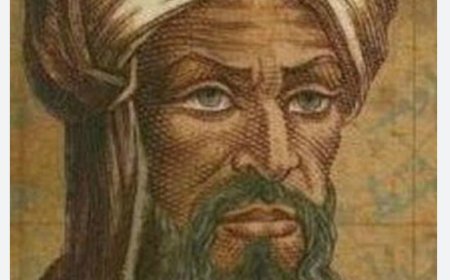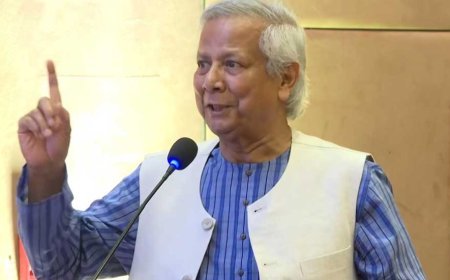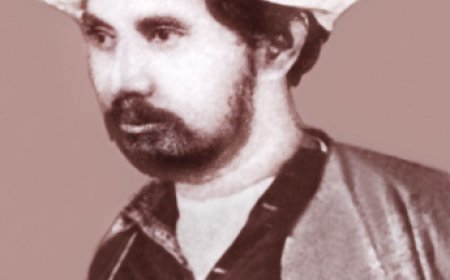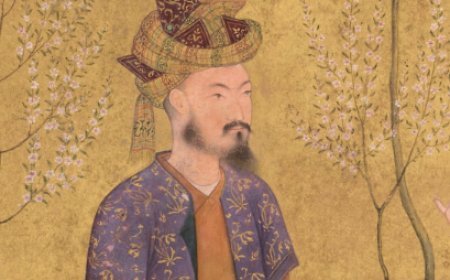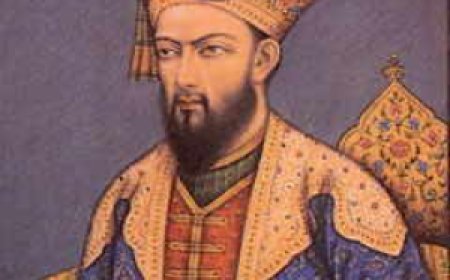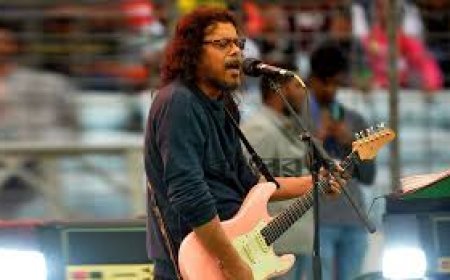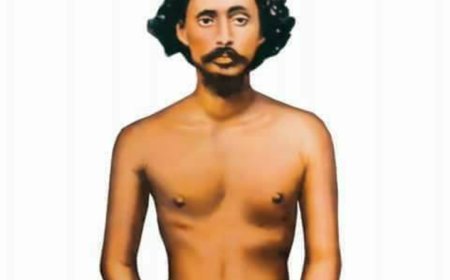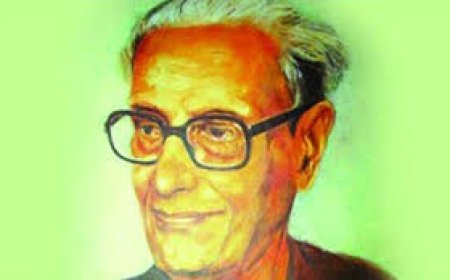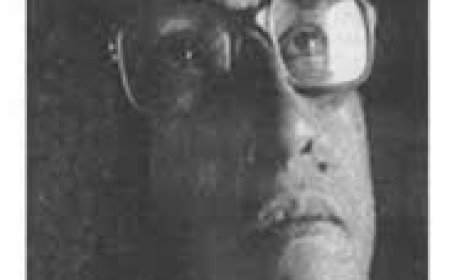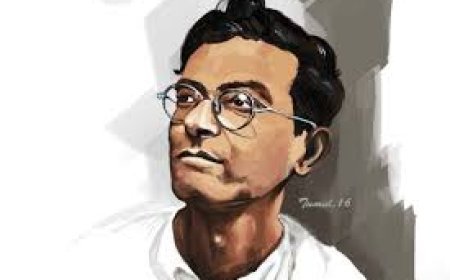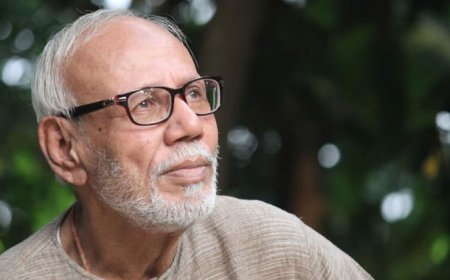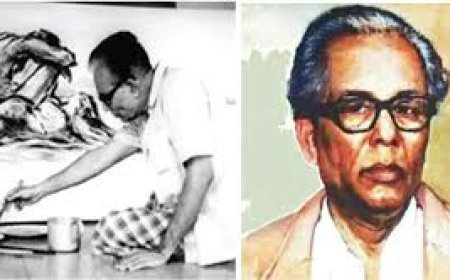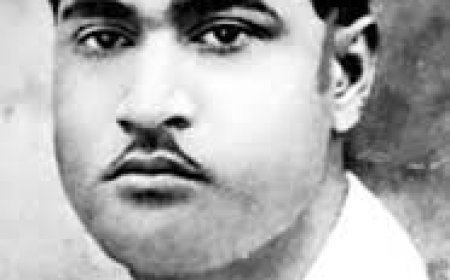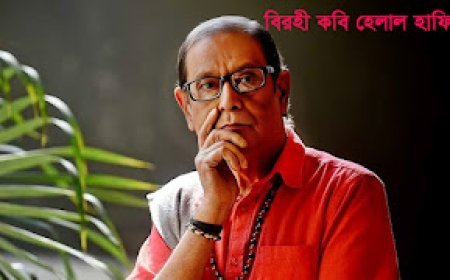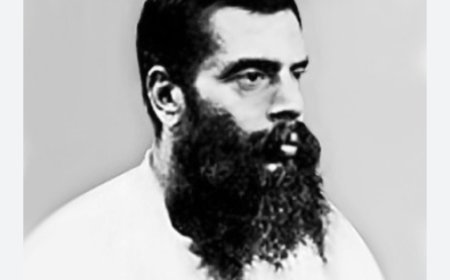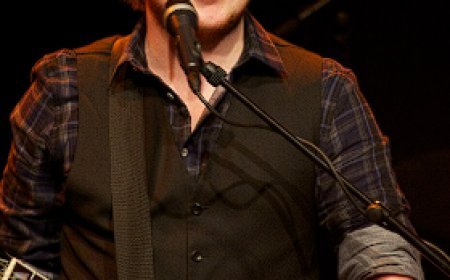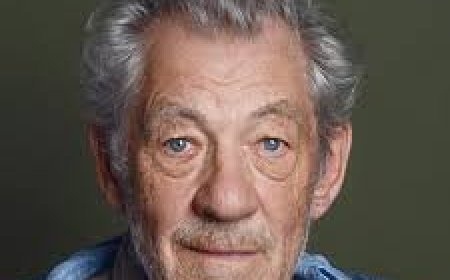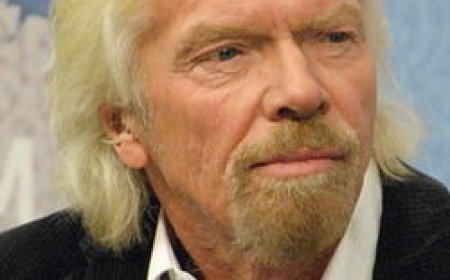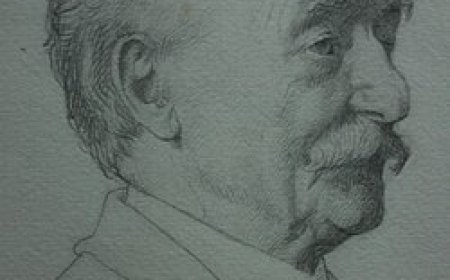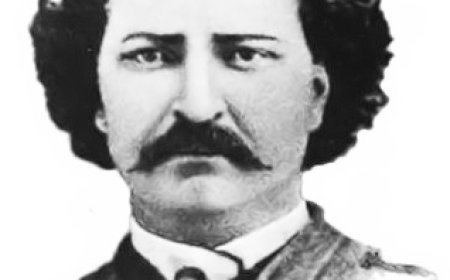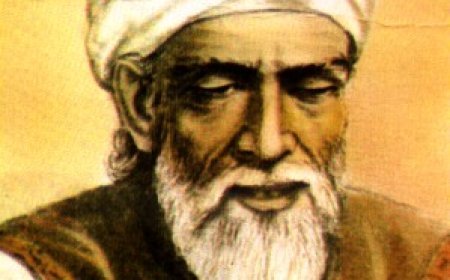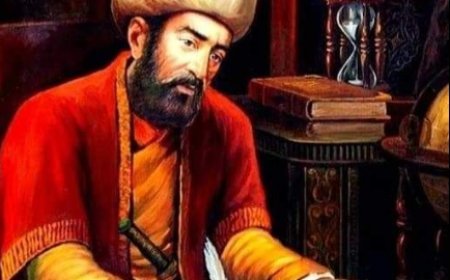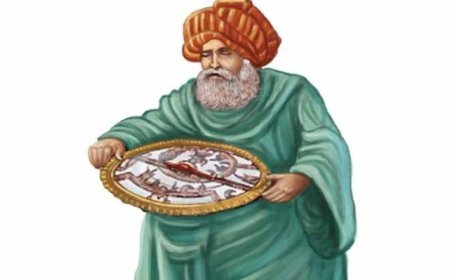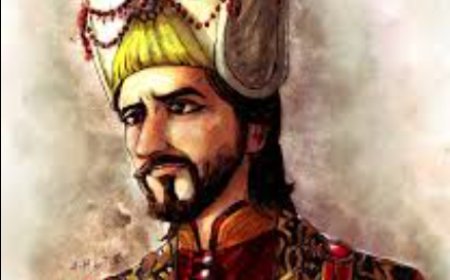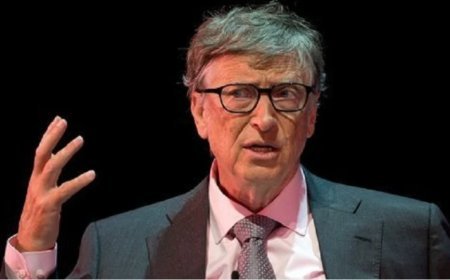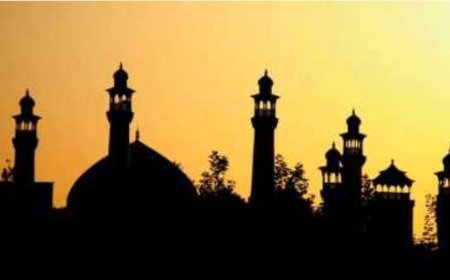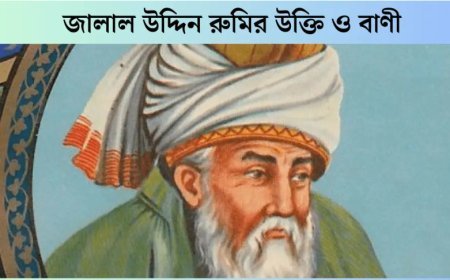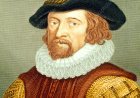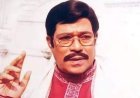রিচার্ড ডকিন্স এর জীবনী | Biography of Richard Dawkins
রিচার্ড ডকিন্স এর জীবনী | Biography of Richard Dawkins
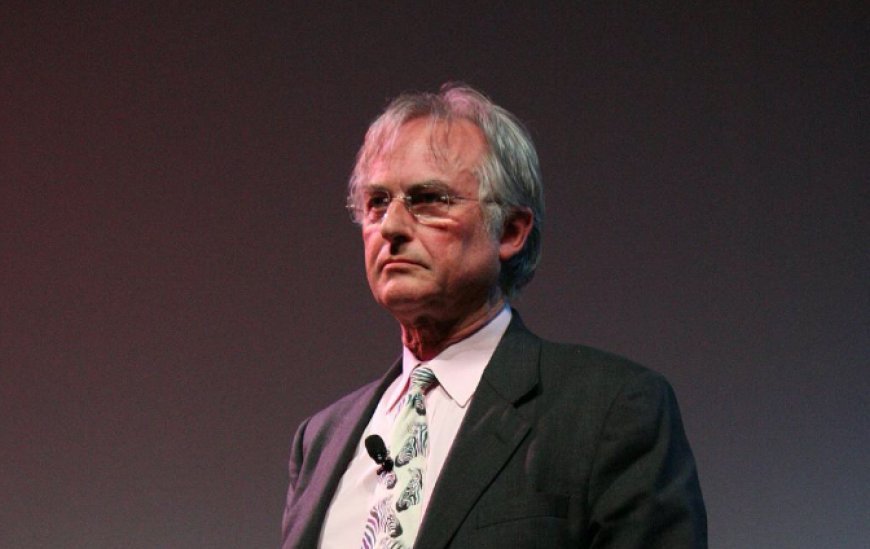
প্রিয় বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স: বিজ্ঞানের ঘোড়সওয়ার
| জন্ম |
ক্লিন্টন রিচার্ড ডকিন্স
২৬ মার্চ ১৯৪১ নাইরোবি, কেনিয়া উপনিবেশ
|
|---|---|
|
জাতীয়তা |
ব্রিটিশ |
|
শিক্ষা |
এমএ, পিএইচডি (অক্সন) |
|
মাতৃশিক্ষায়তন |
Balliol College, Oxford |
|
পেশা |
ইথলোজিস্ট |
|
কর্মজীবন |
১৯৬৭-বর্তমান |
|
প্রতিষ্ঠান |
Fellow of the Royal Society Fellow of the Royal Society of Literature |
|
পরিচিতির কারণ |
Gene-centered view of evolution, concept of the meme, as well as advocacy of atheism and science. |
|
উল্লেখযোগ্য কর্ম
|
The Selfish Gene (1976) The Extended Phenotype (1982) The Blind Watchmaker (1986) The God Delusion (2006) |
| দাম্পত্য সঙ্গী | Marian Stamp Dawkins (m. 1967–1984) Eve Barham (m. 1984–?) Lalla Ward (m. 1992–present) |
|
পিতা-মাতা |
Clinton John Dawkins Jean Mary Vyvyan (née Ladner) |
|
পুরস্কার |
ZSL Silver Medal (1989) Faraday Award (1990) Kistler Prize (2001) |
ক্লিন্টন রিচার্ড ডকিন্স :
(জন্ম: ২৬ মার্চ ১৯৪১) একজন ইংরেজ বিবর্তনবাদ বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস সিম্নোয়ি চেয়ার ইন দি পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সায়েন্স-এ অধিষ্ঠিত ছিলেন; ২০০৮ সালে তিনি এই পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। অধ্যাপক ডকিন্স 'সেলফিশ জিন' গ্রন্থটির জন্য বিদ্বৎসমাজে পরিচিত। তার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বই - এক্সটেডেড ফেনোটাইপ, ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার, রিভার আউট অব ইডেন, ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইম্প্রবেবল, আনউইভিং দ্য রেইনবো, ডেভিলস চ্যাপ্লিন, অ্যান্সেস্টর টেল, দ্য গড ডিলুশন এবং দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। তিনি আধুনিক বিশ্বে সাধারণ মানুষদের মধ্যে বিবর্তনকে জনপ্রিয়করণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।
প্রাথমিক জীবন
ডকিন্স ১৯৪১ সালের ২৬শে মার্চ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার নাইরোবিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা ইয়ান ম্যারি ভিভিয়ান (নি ল্যাডনার) এবং পিতা ক্লিনটন জন ডকিন্স (১৯১৫-২০১০) একজন প্রাক্তন সরকারি কৃষি কর্মকর্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তার পিতা রাজার আফ্রিকান রাইফেলে যোগ দানের জন্য ডাক পান। এবং ১৯৪৯ সালে ডকিন্সের বয়স যখন ৮ বছর, তখন তিনি ফিরে আসেন। অক্সফোর্ডশায়রে ডকিন্সের বাবা উত্তরাধিকার সূত্রে বেশ কিছু জমি পেয়েছিলেন, যা তিনি কৃষিকাজে ব্যবহার করতেন। ডকিন্স নিজেকে ইংরেজ দাবী করেন এবং ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে বাস করেন। ডকিন্সের একজন ছোট বোন আছে।
ডকিন্সের পিতামাতা দুইজনই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন এবং তারা সব সময়ই ডকিন্সের প্রশ্নের বৈজ্ঞানিকভাবে উত্তর দিতেন। ডকিন্স নিজের শৈশবকে আর দশজন সাধারণ ইংরেজদের মতোই বলেছেন। তিনি টিনেজ বয়স অব্দি খ্রিষ্টান ধর্মালম্বী ছিলেন কিন্তু এক পর্যায়ে তিনি অনুভব করেন আধুনিক বিবর্তনবাদ তার জীবনের জটিলতাকে আরো সহজভাবে ব্যাখ্যা করে এবং তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে সরে আসেন।
ডকিন্স বলেন, "প্রাণের জটিলতা দেখে এর সবকিছুর একজন স্রষ্টা আছেন ভাবতে সহজ হয় বলেই আমি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু, আমি মনে করি, যখন আমি বুঝতে পারলাম, ডারউইনিজম এই জটিলতার আরো উন্নত ব্যাখ্যা দেয় তখন তা আমাকে সৃষ্টিতত্ত্বের জাল থেকে বেড়িয়ে আসতে সাহায্য করলো।
দ্য সেলফিশ জিন দিয়ে রিচার্ড ডকিন্সের পাঠ শুরু করেছিলাম। টিঙটিঙে একটা বইয়ের ভেতর এতখানি বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো আমার পাতা উল্টে যাবার জন্যে, বুঝিনি। ডকিন্স খুব মৃদু কণ্ঠে যেন বিরাট এক গর্জন করে গেলেন আমার মনের ভেতর। বিবর্তনের অসংখ্য প্রশ্নময় পৃথিবীতে আমি শিশুর মতো টলমল করে প্রবেশ করলাম।
ডকিন্সের পরবর্তী যে বইটি আমার টানা কয়েক সপ্তাহের সঙ্গী, সেটি তাঁর ম্যাগনাম ওপাস, দ্য অ্যানসেস্টর'স টেল। ক্যান্টারবেরি টেলস এর আদলে সেখানে বিবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করে বিভিন্ন প্রজাতি, প্রত্যেকেরই একটি করে গল্প আছে বলার। চলার পথে এক এক করে সে যাত্রায় যোগ দিতে থাকে পূর্বপুরুষেরা, কাহিনী বাড়তে থাকে, যোগ হতে থাকে অসংখ্য প্রশ্ন, যোগ হতে থাকে উত্তর, ইঙ্গিত, চিন্তার খোরাক। ডকিন্সের এই বইটি পড়ে আমি প্রবল আলোড়িত হয়েছিলাম, মনে হয়েছিলো, বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে এমন একজন লেখকের খুব প্রয়োজন ছিলো। বিশ্বের ষষ্ঠ ভাষা হয়েও বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়, পাঠকের অভাবে বাংলা ভাষা যেন শুধু বাতাসে ভাসে, হরফে ফোটে না।
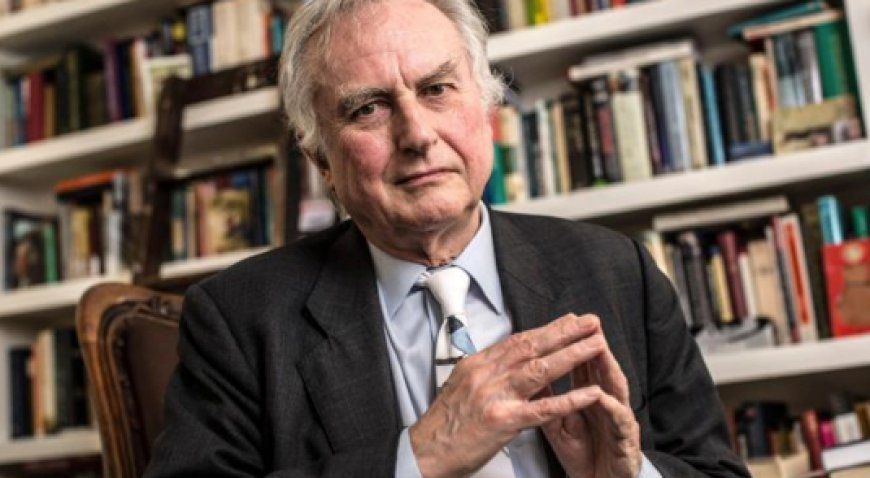
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিংস আফ্রিকান রাইফেলসে যোগ দেওয়ার জন্যে তার যখন ডাক পড়ে তখন রিচার্ডের
মাত্র ৮ বছর বয়স। তাই বাবার সাথে রিচার্ড ও ইংল্যান্ডে ফিরে অক্সফোর্ডশায়ারের ওভারনর্টন পার্কে নিজেদের পৈতৃক বাড়িতে ফিরে আসেন। ছোট বোনের সাথে সেখানেই তিনি তার ছেলেবেলা কাটান।
তার বাবা মা দু’জনেই বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই ডকিন্সের কৌতূহলী মনের উত্তরগুলি বাবা মায়ের কাছ থেকে বিজ্ঞানের আলোকেই পেতে শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার প্রতি ডকিন্সের অন্যরকম আগ্রহ ছিল। মহাবিশ্বের বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে পড়তে তার খুব ভাল লাগত। কিন্তু ছেলেবেলার একটা বিরাট সময় পর্যন্ত তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন এবং নিজেকে পরিচয় দিতেন “এঞ্জেলিক্যান ক্রিশ্চিয়ান” হিসেবে। কিন্তু একটু বেড়ে ওঠবার পর স্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে তিনি যখন ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়তে সুযোগ পান তখন থেকেই তার ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিকে হতে শুরু করে।
ডকিন্স বলেছেন,
“এই মহাবিশ্বের বিস্ময় দেখে আমার এক সময় একজন মহানির্মাতার ছবি মনে আসত। ডারউইনের বিজ্ঞান পড়ার পর, সেই ছবি মন থেকে উধাও হয়ে যায়।”
স্কুলে পড়ার সময় তিনি বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখা “ আমি কেন ক্রিশ্চিয়ান নই ” বইটি পড়েছিলেন। এই বই ছোটবেলা থেকেই তার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অক্সফোর্ডের ব্যালিয়ল কলেজ থেকে ১৯৬২ সালে তিনি প্রাণিবিদ্যায় স্নাতক অর্জন করেন। এখানে থাকার সময়ই নোবেল বিজয়ী প্রাণী আচরণতত্ত্ববিদ নিকোলাস টিনবার্জেন এর ব্যক্তিত্ব তাকে অনুপ্রাণিত করে। তাই টিনবার্জেনের অধীনে এখানেই তিনি তার এম এ এবং পি এইচ ডি সমাপ্ত করেন।
কর্মজীবনের শুরুতে ডকিন্স বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ঠিক এরকম সময়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধের প্রতিবাদে তিনি সামিল হন। ১৯৭০ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকাচারার পদে যোগ দেন। ১৯৯০ সালে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের রিডার এবং ১৯৯৫ সালে তিনি “বিজ্ঞান এর সার্বজনীন প্রচার ও প্রসার” বিষয়ে সিমোনয়ি অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেখানেই তিনি তার অবশিষ্ট অধ্যাপনা জীবন ব্যয় করেন।
একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে , বিজ্ঞান গবেষণায় পেশাগত দক্ষতা থাকলেই সবসময় তার বিজ্ঞান সংস্কৃতি সঠিক পথের অনুসারী হয়না। তাই ডকিন্সের ধর্ম ও বিজ্ঞান দর্শন সম্পর্কিত যে মতবাদ সেটি কয়েকজনের কাছে যেমন মেনে নিতে কষ্ট হয় তেমন ই বিজ্ঞান জগতের অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্রের সমর্থন পেয়েছেন তিনি। হ্যারল্ড ক্রোটো, জেমস ওয়াটসন, স্টিভেন ভেইনবার্গের নাম ও রয়েছে এই তালিকায়।
ছোটবেলায় যে “মহানির্মাতা” র ধারণা তার মনে ছিল সেই ধারণা নস্যাৎ করতে তিনি পরিণত বয়সে এসে কলম ধরেছেন। কলম ধরেছেন সকল ধরণের ধর্মীয় বিশ্বাস, অন্ধভাবে চলতে থাকা আইন কানুনের বিরুদ্ধে। তার লেখনী অসম্ভব তীব্র।
রিচার্ড ডকিন্স নেচার, সায়েন্স প্রভৃতি বিখ্যাত গবেষণা পত্রিকায় একের পর এক সাড়া জাগানো গবেষণাপত্র প্রকাশকারী বিজ্ঞানীই শুধু নন। তিনি সমসাময়িক কালের একজন অসাধারণ সাহিত্যিক ও। ২০০৫ সালে তাই তিনি শেক্সপিয়র পুরস্কার লাভ করেন। তার লেখায় বিবর্তনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি জটিল বিষয়ও ফুটে উঠেছে অপূর্ব সহজবোধ্যতায়। তিনি যেন বিজ্ঞানের সৌন্দর্যকে সকলের হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতেই আবির্ভূত হয়েছেন। তাই পাশাপাশি তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিবর্তনবাদ থেকে শুরু করে জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দিয়েছেন বক্তৃতা। ধর্মের অসারতা প্রমাণ করতে রচনা করেছেন দুর্দান্ত কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র। ছুটে গেছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। নাস্তিকতা ও যুক্তিবাদকে তিনি মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন স্পষ্ট ভাষায়, বিজ্ঞান ও যুক্তির মেলবন্ধনে , প্রকৃতিবিজ্ঞানের সৌন্দর্যের মিশেলে। তিনি তার লেখায় নাস্তিকতার সংজ্ঞাকে রূপায়িত করেছেন এভাবে,
“ একজন নাস্তিক ব্যক্তি এই অর্থে দার্শনিক প্রকৃতিবাদী যিনি মনে করেন প্রকৃতি ও পার্থিব জগতের বাইরে কিছু নেই, দৃশ্যমান মহাবিশ্বের অন্তরালে ওৎপেতে থাকা অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিশীল কোন বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব নেই, দেহাতীত আত্মা নেই এবং নেই কোন অলৌকিকতা – ব্যত্যয় কেবল যে এমন কিছু প্রাকৃতিক প্রতিভাস রয়েছে যা আমরা এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারি নি। যদি এমন কোন অবোধ্য ঘটনা থাকে যা আমাদের কাছে এখনও ব্যখ্যাতীত, আমরা মনে করি অদূর ভবিষ্যতে এর রহস্য উন্মোচিত হবে, এবং তা প্রাকৃতিক ব্যখ্যার পরিমণ্ডল থেকেই। আমরা যখন রংধনুর রহস্য ভেদ করি, এর অপার সৌন্দর্য -চমৎকারিত্ব কিন্তু বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না।”
রোমান ক্যাথলিকেরা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নন। এরকম হাস্যকর ধারণা নিয়ে বিভিন্ন মধ্যযুগীয় মানুষ আজ ও বেঁচে আছেন ও তাদের সেই বিষাক্ত চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটাচ্ছেন বিভিন্ন সমাজে। এরকম অনেকে আছেন নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন না , অনেকে অসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। ধর্মান্ধ গোঁড়া মধ্যযুগীয় এইসব মানুষদের বিরুদ্ধে ডকিন্স তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধী ছিলেন তিনি। ইরাকে মার্কিনীদের অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে রিচার্ড ডকিন্স জর্জ বুশ জুনিয়রকে একাধিক চিঠি লেখেন। সেই চিঠি সাম্রাজ্যবাদী , বীরপুরুষের মোড়কে লুকিয়ে থাকা এক কাপুরুষতার প্রতিভূ বুশকে কে সারা বিশ্বের সামনে আরেকবার মাথা নত করতে বাধ্য করেন। সেই চিঠিতে যেরকম স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল আজকে বিভিন্ন টেলিভিশনে আসা বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী যারা মিনিটে মিনিটে নানা রকমের যুক্তিহীন ও ইনিয়ে বিনিয়ে ভণ্ডামো ও ভাঁড়ামোর বিভিন্ন বক্তব্য প্রসব করেন তা কল্পনাও করতে পারবেন না ।
সেলফিশ জিন নামের বৈপ্লবিক গ্রন্থ দিয়ে শুরু। তারপরে একে একে রিচার্ড ডকিন্সের হাত ধরে এই বিশ্ব পেয়েছে অনবদ্য কয়েকটি গ্রন্থ। গড ডিল্যুশন, ম্যাজিক অফ রিয়েলিটি , ব্লাইন্ড ওয়চমেকার, আনইভিং দ্য রেইনবো, এক্সটেণ্ডেড ফিনোটাইপ – এগুলি তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পাশাপাশি তার আত্মজীবনী বের হয়েছে দুটি খণ্ডে- “ এপেটাইট ফর ওয়ান্ডার” এবং “ ব্রিফ ক্যান্ডেল ইন দ্য ডার্ক”। গড ডিল্যুশন ও ম্যাজিক অফ রিয়েলিটি বই দুইটি বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে । কাজী মাহবুব হাসানের অনুবাদে গড ডিল্যুশন প্রকাশ পেয়েছে অনার্য প্রকাশনী থেকে। ম্যাজিক অফ রিয়েলিটি সিরাজাম মুনির শ্রাবণ অনুবাদ করেছেন “বাস্তবতার যাদু” শিরোনামে। এটি প্রকাশিত হয়েছে রোদেলা প্রকাশনী থেকে।
২০০৬ সালে গড ডিল্যুশন বইটির জনপ্রিয়তা তাকে “রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেষন ফর রিজন এন্ড সায়েন্স” সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। যুক্তি ও বিজ্ঞান চিন্তার প্রসার এই সংগঠনের প্রধান কাজ। আমেরিকার অনেক স্থানে আজও বিবর্তনবাদ পড়ানো হয় না। কোথাও কোথাও সৃষ্টিবাদীদের কুচক্রান্তে পড়ানো হয় ইনটেলিজেন্ট ডিজাইন নামের তৃতীয় শ্রেণির আবর্জনা। এই আবর্জনা যেন বিজ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীদের কোনভাবেই প্রভাবিত না করতে পারে সেজন্যে এই সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে নিরন্তর।
রিচার্ড ডকিন্স আরও অনেক দিন বেঁচে থাকুন । সুস্থ থাকুন । কাজ করে যান নিরন্তর। সকল ধরণের ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার কে ধ্বংস করতে থাকুন নিয়ত। শুভ জন্মদিন বিজ্ঞানের জাদুকর। এক সাধারণ গুণমুগ্ধের বিনয়াবনত নমস্কার গ্রহণ করুন। পাশাপাশি শ্রদ্ধা গ্রহণ করুণ হুমায়ুন আজাদ, অনন্ত বিজয় দাশ, অভিজিত রায়ের মত বাঙালি মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী চেতনার পথিকৃতেরা যাদের আমরা বড্ড অসময়ে হারিয়ে ফেলেছি।
What's Your Reaction?
 Like
0
Like
0
 Dislike
0
Dislike
0
 Love
0
Love
0
 Funny
0
Funny
0
 Angry
0
Angry
0
 Sad
0
Sad
0
 Wow
0
Wow
0